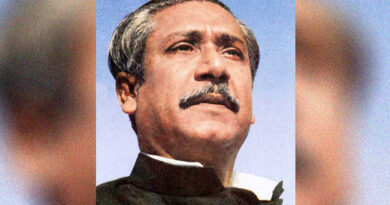সিস্টেম বদলালে দেশ বদলাবে
সিস্টেম ভালো মানে দেশ উন্নত। একটি দেশের উন্নতি কিংবা জীবনব্যবস্থার উন্নয়নের ভিত্তি নির্ভর করে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক দ্বারা নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভিত্তিতে। তাই লিখতে বসলাম সিস্টেমের কিছু গলদ নিয়ে। প্রথমে আসি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ হলো, আমরা শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করাই। কম্পিউটার কত সালে আবিষ্কৃত হয়? আর বিশ্বের ইউরোপ, আমেরিকার মতো উন্নত দেশে শিক্ষার্থীদের শেখায় প্রগ্রামিং।
আমরা অনার্স-মাস্টার্স শেষে একটি চাকরির আশায় নেমে আসি নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাস মুখস্থ করতে। আর তারা অনার্স-মাস্টার্সে পড়ার সময় স্ব-স্ব বিষয়ে কর্মমুখী হতে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হলো অনেকটা এলোমেলো। পড়ালেখার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের মিল নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে দেশের টেকসই উন্নয়ন কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচ্ছন্নতা আনা পুরোপুরি সম্ভব নয় বলে মনে করি। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন জরুরি। রাষ্ট্রীয় খরচে প্রতিটি কাজের জন্য প্রতিটি বিভাগের জন্য দক্ষ লোক তৈরি করতে বিদেশে টিমভিত্তিক পড়াশোনা কিংবা প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতে হবে। তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বদেশিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
কিছুদিন আগে আলু চাষ দেখতে, পুকুর খনন দেখতে কিছু কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণে আসতে দেখে মানুষ হাসত। কিন্তু আসল কথা হলো, ইউরোপ-আমারিকায় এই কাজগুলো আমাদের দেশের মতো সনাতন পদ্ধতিতে হয় না। আমি মনে করি, তাই তাদের এগুলো দেখতে আসা উচিত।
এবার আসি দেশের আইনের শাসনব্যবস্থা নিয়ে। খবরের কাগজ খুলেই দেখি ধারাবাহিক অশান্তির খবর। দেশে আইনের শাসন নিশ্চত করতে না পারলে আপনি বা আপনারা আক্রান্ত হবেনই। জার্মানিতে একজন মেয়র কিংবা মন্ত্রী নিজ দায়িত্ব পালন শেষে সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তাঁর চলাফেরা। সবার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ও বাসে চড়েন। নেই কোনো নিরাপত্তা প্রটোকল।
কিন্তু আমাদের দেশে কি তা সম্ভব? উত্তর হলো- না। এ ছাড়া আমাদের যেমন আইন রয়েছে, তেমনি তাদেরও আইন রয়েছে। পার্থক্য হলো, ইউরোপীয়রা আইন মানতে বাধ্য, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই আইনের প্রয়োগ হয়। আর আমাদের মধ্যে রয়েছে বিলম্বিত করার অভ্যাস এবং আইনের অপপ্রয়োগসহ স্বজনপ্রীতি। যার কারণে রাষ্ট্রের সবাই কমবেশি ভুগছে। মোট কথা, এখনই সময় সিস্টেম বদলানোর। সিস্টেম বদলানো গেলে রাষ্ট্র বদলাবে। প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখবে।
পৃথিবীর প্রায় দেশে সরকারি কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয় স্ব-স্ব পদের যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞদের। একজন ব্যাংকার নিয়োগ দেবেন, তাকে হতে হবে ওই বিষয়ে পড়াশোনা ও কর্ম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আমাদের দেশে নেওয়া হচ্ছে বাংলা, সাধারণ জ্ঞান, অঙ্ক-এই টাইপের ওপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এখন কথা হচ্ছে, এভাবে স্ব-স্ব কাজের পড়াশোনা বা অভিজ্ঞতা না নিয়ে যদি নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্র কিভাবে সামনে যাবে? রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের এখনই ভাবতে হবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন জরুরি। একজন ডাক্তারকে তার নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কেন মুখস্থ করতে হবে রবিঠাকুরের হৈমন্তী গল্পের গৌরী সংকর বাবু কোথায় বাস করেছিলেন? ঠিক একইভাবে একজন ইংরেজির শিক্ষককে কেন মুখস্থ করতে হবে যে বিদ্যা+আলয় মিলে বিদ্যালয় হয়। সাহিত্যে পড়াশোনা করে কেন অডিটে চাকরি করবে? ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সে কেন কাস্টমসে চাকরি করবে?
এখনই সময় ভাবার ও বোঝার। চিন্তা করতে হবে সুদূরপ্রসারী। ভাবতে হবে, আগামী ৫০ বছর পর রাষ্ট্র কোথায় যাবে? একটু ভেবে দেখুন, ইউরোপের কথা বাদই দিলাম। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি কোথায় আর আমরা কোথায়? কেন আমরা পেছনে? কারণ সিস্টেমের ভুল, অনিয়ম বা দুর্নীতি। সিস্টেম বদলালে দুর্নীতি ও অনিয়ম পালাবে। যেমন জার্মানির উদাহরণই দিই। এখানে মানুষ রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে পারে না। কারো সম্পদ বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপযুক্ত কারণ দেখানোর নোটিশ দেওয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার ও অনলাইনে মনিটরিং হয়। নেই কোনো প্রশাসনিক জটিলতা।
আরেকটি বিষয়, সেটি হলো আমাদের ডাক বিভাগ। যেটি আজ মৃতপ্রায়। অথচ জার্মানির ডাক বিভাগ পৃথিবী বিখ্যাত। কারণ স্বচ্ছতা ও সেবার মান। আমাদের ডাক বিভাগকে প্রাণে ফেরাতে হবে। প্রথমে প্রাণ ফিরে পেতে ডাক বিভাগকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি কুরিয়ার সেবা চালু করতে হবে। তাহলে ডাক বিভাগ একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেবে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ডাক বিভাগে কুরিয়ার সেবা চালু আছে।
এবার আসি বাংলাদেশের রেলওয়ের কথায়। প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ টিকিট পায় না। যার কারণ, অসাধু কর্মকর্তাদের সহায়তায় টিকিট কালোবাজারিদের হাতে চলে যায়। ভেবে দেখুন, একটু সিস্টেমের পরিবর্তন করলে এটি সহজেই বন্ধ করা যাবে। এই সিস্টেম বদলাতে ইউরোপ আসতে হবে না- সিঙ্গাপুর কিংবা ব্যাংককের দিকে খেয়াল করুন। প্রতিটি রেলস্টেশনে রয়েছে টিকিট কাটার জন্য ভেন্ডারিং মেশিন। দেখতে হুবহু ব্যাংকের এটিএম মেশিনের মতো ভিসা কার্ড কিংবা টাকা মেশিনে ঢুকিয়ে দেবেন অটো, যার টিকিট সে কেটে নেবে। দরকার হবে না লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিটের জন্য হাহাকার করার। কালোবাজারি থেকে টিকিট কাটার জন্য এনআইডি নাম্বার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও যার টিকিট সে কাটতে পারবে, শিশুদের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন নাম্বার দিয়েও কাটার সিস্টেম করা যেতে পারে। তাহলে অনেকটাই কালোবাজারিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।
আমাদের দেশে রাস্তায় যেখানে-সেখানে ময়লা। আর ইউরোপের রাস্তাঘাট আয়নার মতো পরিষ্কার। আমাদের নয় কেন? আমি বলব, সিস্টেমে কিছু ভুল। বিভিন্ন সেন্টারে কিছুদূর পর পর বড় বড় ময়লা সংগ্রহের বক্স বসিয়ে দিন, যেখানে একসঙ্গে তিনটি পার্ট থাকবে- একটিতে কাগজ, অন্যটিতে ব্যবহৃত বোতল এবং আর একটিতে খাবারের বর্জ্য। মানুষ বক্স দেখে রাস্তাঘাটে আর ময়লা ফেলবে না এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পরিবহন করতে হবে এবং ময়লা নিয়ে নতুন পলিব্যাগ বসিয়ে দিতে হবে। এখন কথা হলো, আমরা ময়লা ফেলা বক্স দিয়েছি অর্ধকিলোমিটার পর পর, আবার অনেক শহরে ময়লা ফেলার বক্সও নেই। তাহলে মানুষ তো ময়লা রাস্তায় ফেলবেই। সঙ্গে রাস্তা দ্রুত পরিষ্কারের জন্য আধুনিক মেশিন ব্যবহার করতে হবে।
রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি চলাকালে ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যবহার কমাতে হবে। ইউরোপের কোনো দেশে চাকরি চলাকালে মোবাইল ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেউ ব্যবহার করতে পারে না। এমনকি আপনি দেখবেন, ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় দেশে ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি চলাকালে বসার নিয়ম নেই। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেবা দেন।
দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে বেকার বানানোর কারখানায়। প্রতিবছরই দু-একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে আর বের হচ্ছে কয়েক হাজার বেকার। দল বেঁধে পড়ানো হচ্ছে, যার সঙ্গে বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রের কোনো মিল নেই। এত বেকারের ভিড়ে চাকরি বাংলাদেশে একটি সোনার হরিণ। কম্পানিরাও এটা বোঝে। ফলে এই দেশের শিক্ষিত ছেলেরা প্রত্যাশা অনুযায়ী বেতন পায় না, চাকরি পায় না; পেলেও সহ্য করতে হয় মালিক অথবা বসের নানাবিধ অদ্ভুত পরীক্ষা ও অপেশাদার আচরণ। আমরা মনে করি স্যুট, টাই পরে কোনো কাজ করতে পারলেই বুঝি সেখানেই জাতির সফলতা। এটা আসলে একটি অপ্রকাশ্য দৈন্য, যা কেউ স্বীকার করছে না। এই দেশের অর্থনীতি প্রসিদ্ধ করতে চাইলে আমাদের উচিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনসহ কর্মমুখী শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া।